 |
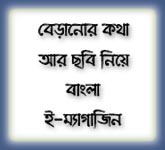 |
|
|
|
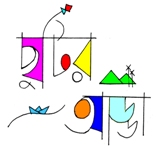
বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।
কলকাতার কাছেই
রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা মহানগরীর জনারণ্য ছাড়িয়ে দক্ষিণে হুগলী নদীর পূর্বতীরের একটি শান্ত জনপদ পূজালি।
এক বর্ষার মেঘলা দুপুরে বাওয়ালি রাজবাড়ি যাওয়ার পথে হাজির হয়েছিলাম পূজালির নেতাজী পার্কে। বিস্তৃত গঙ্গা যেখানে বাঁক নিয়েছে ডায়মন্ড হারবারের দিকে, সেখানেই পূজালি গ্রাম, পৌরসভা।
মেঘলা দুপুরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় সবুজ প্রকৃতির বুকে নদীতট সংলগ্ন একখণ্ড সাজানোগোছানো পিকনিক স্পট এই নেতাজী পার্ক। সার দেওয়া গ্যারেজ আছে গাড়ি রাখার জন্য, এখন সবকটিই ফাঁকা, কিন্তু শীতকালে এ জায়গাটা যে শহুরে ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে সরগরম থাকে তা জানালেন আমাদের ড্রাইভার গোরা নাইয়া।

বাঁধানো ঘাটের রেলিং থেকে বিস্তারিত গঙ্গার ঘোলাজলে ডিঙি নৌকার ভেসে চলা দেখতে দেখতে হেঁটে বেড়ালাম তীর ছুঁয়ে গাছগাছালি, কৃত্রিম পশুপাখি, দোলনা দিয়ে সাজানো পার্কে।
আকাশ থেকে মেঘেরা তখন ঝরিয়ে দিল কয়েকফোঁটা বাদল অশ্রু। পূজালিকে পেছনে ফেলে গাড়িতে চললাম আজকের মুখ্য গন্তব্য বাওয়ালি রাজবাড়ির দিকে।
কাঁটারিয়া, ভাতহেঁড়িয়া বাজার, ছবির মোড়, মোহনপুর, নস্করপুর মোড় পেরিয়ে এসে নোদাখালি হাট, চাউলখোলার ছোট ছোট বাজার, স্কুল, গ্রাম পার হয়ে বর্ষার মেঘসহ ঘন সবুজ গাছে ছাওয়া গ্রাম্য পথ বেয়ে বাওয়ালি মোড়ে পৌঁছে পথচারীদের কাছে পথ নির্দেশ পেয়ে গাড়ি এগোল কয়েকশত বছরের পুরোনো বাওয়ালি রাজবাড়ির দিকে।
মুঘল আমলে বাংলার সম্রাট আকবরের একজন সেনাপ্রধান ছিলেন মাহিষ্য সম্প্রদায়ের শোভা রাম রাই। মূলত উত্তর প্রদেশ থেকে এসে কৃষক ও জলদস্যুদের বিদ্রোহ দমন করার বিনিময়ে তিনি বঙ্গদেশে তিন লক্ষ একর জমি উপহার পেয়েছিলেন। কিংবদন্তি আছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমে এবং পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে রাই পরিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, হুগলি নদীর পাশে এই এলাকাতে নিজেদের সম্পদের উন্নতি করে। আগে এই এলাকা সুন্দরবনেরই একটি অংশ ছিল। ম্যানগ্রোভের প্রসারিত জলাভূমি, অগণিত বাঘ এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। স্থানীয় জনগণ ছিল বাউল সম্প্রদায়, বনবাসী, যারা জীবিকা নির্বাহ করত, মাছ ধরা এবং মধু সংগ্রহ করে। দুটি প্রধান দেবতার পূজা করত তারা – 'বন বিবি' বা বনের দেবী এবং 'দক্ষিণ রায়' বা বাঘের দেবতা, দুজনেই তাদের রক্ষা করবেন।
সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে শোভারাম রাই মন্ডল উপাধিতে ভূষিত হন। শোভারামের নাতি রাজারাম হিজলির সেনাপতি থাকাকালীন সাহসিকতার জন্য পঞ্চাশটি গ্রামের মালিকানা পেয়েছিলেন, যার মধ্যে বাওয়ালি আর বজবজও ছিল। রাজারামের নাতি হারাধন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসার অংশীদার ছিলেন। সেইসময় হারাধনের ছেলেরা বাওয়ালিতে বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করে জায়গাটাকে মন্দিরনগরী করে গড়ে তোলেন।
মন্ডল পরিবার ছিলেন ভগবান কৃষ্ণের উপাসক। বসতি স্থাপন করে প্রথমেই তাঁরা 'শ্রী রাধাকান্ত জিউ' মন্দির তৈরি করেছিলেন। এরপর এলাকার আশেপাশে আরও কয়েকটি মন্দির গড়ে ওঠে একই স্থাপত্যরীতিতে।
কথিত আছে রানি রাসমণির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যোগাযোগ থাকায় বাওয়ালির গোবিন্দ জিউ-র মন্দিরের আদলে নির্মিত হয় দক্ষিণেশ্বর-এর ভবতারিণী মন্দির। পৌঁছে গেলাম ভগ্নপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর মাঝখানে রাজবাড়ির দোরগোড়ায়। পাশেই সংরক্ষিত গোবিন্দ জিউ-র মন্দিরের চূড়া আর লাগোয়া প্রাচীন পোস্ট অফিস।
গাড়ি দাঁড়াতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলাম। উর্দিপরা এক দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিতে লালপাড় শাড়ি পরা দুই মহিলার একজন শাঁখ বাজিয়ে অপরজন ফুল, প্রদীপ, নানা উপাচারে সাজানো থালা আমাদের সামনে আরতির আঙ্গিকে ঘুরিয়ে, মাথায় ঠেকিয়ে বরণ করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।
মূল দরজার থামের গায়ে ভগ্ন ইটের পাঁজা, দোতলা রাজবাড়ির প্রধান দরজার ভেতরের দুই পাশে তিনটে করে বড়ো প্রদীপ জ্বলছে। ওপরে তালপাতার পাখা ঝুলিয়ে অন্দরসজ্জায় সাবেকিয়ানা।

বাড়ির অভ্যন্তরে প্রশস্ত উঠোন, নাটমন্দির, যার তিনদিকে দোতলা বাড়ির থামওলা বারান্দা, সারি সারি ঘর। রঙহীন সাদা আর মাঝে মাঝে চুনসুড়কির লাল পাঁজর বের করা দেওয়াল। পুরোটাই প্রাচীনত্বকে ধরে রাখার অপূর্ব প্রয়াস। দোতলার ছাদে আসন্ন দুর্গাপূজার প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। আলপনা আঁকা উঠোনের একদিকে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ঠাকুর দালানের দিকে। সেই দালানের ওপরে এখন হয়েছে অতিথিদের জন্য শীততাপনিয়ন্ত্রিত ভোজনালয়।
আমরা উঠোনে আসতেই আরও দুজন লালপাড় শাড়ি পরা মহিলা বড় থালায় করে মাটির গ্লাসে লেবুর জল দিয়ে স্বাগত জানালেন। সেই স্নিগ্ধ লেবুর জল খেয়ে আমরা রাজবাড়ি ঘুরে দেখতে লাগলাম।
প্রায় আড়াইশো বছর আগে নির্মিত রাজবাড়িটি স্থাপত্যের একটি অসাধারণ নিদর্শন। দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে জমকালো জীবনযাপন, পার্টি এবং বিশিষ্ট অতিথিদের আনাগোনা ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পরে, জমিদাররা তাদের বেশিরভাগ সম্পদ হারিয়েছিল এবং বাড়িটি দুর্দশার মধ্যে পড়তে শুরু করেছিল। পরিবারগুলি তাদের নিজেদের জীবিকার জন্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কয়েকজন সদস্য তাঁদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে অর্থসংগ্রহের জন্য, এটিকে চলচ্চিত্রের শুটিং এবং সিনেমা থিয়েটার হিসাবে ভাড়া দিতে শুরু করেন।
সেই সময় অজয় রাওলা নামে এক অবাঙালি শিল্পপতি রাজপরিবারের সন্তান অরুণ মন্ডলের কাছে ভেঙে পড়া রাজবাড়িটি কিনে নেন। তিনিই ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে চলে যাওয়া এই রাজবাড়ি, বাওয়ালি জমিদারদের ঐশ্বর্য, শৈলী এবং অনুগ্রহ প্রতিফলিত করার জন্য সংরক্ষণ এবং চমৎকারভাবে পুনরুদ্ধার করে এটিকে একটি শুটিং স্পট, রিসর্ট, এবং বাঙালির সপ্তাহান্তিক ভ্রমণের উপযুক্ত গন্তব্য হিসেবে তৈরি করেন।
এখন প্রায়ই বিভিন্ন সিনেমার শুটিংয়ে রাজবাড়িটি ব্যবহার করা হয় উপযুক্ত আর্থিক মূল্যের বিনিময়ে। আমাদের সঙ্গে কলকাতার বেশ কিছু পরিবার এসেছিলেন, যারা কেউ কেউ এখানে ঘর নিয়ে দুদিন কাটাচ্ছেন ছায়া সুনিবিড় প্রকৃতির কোলে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর প্রাচীন রাজবাড়ির অন্দরমহলে।
উঠোনের একপাশ দিয়ে পেছনের পুকুরপাড়ে দেখা পেলাম একদল রাজহাঁসের। পুকুরের জলে তাকাতেই ঝাঁকে ঝাঁকে রুই কাতলাকে সানন্দে ভেসে বেড়াতে দেখলাম।
একটু এগিয়েই অতিথিদের বাথরুমের আয়না, ঝাড়লণ্ঠন সবেতেই যেন কোন সুদূর অতীতের ছোঁয়া। লাল সিমেন্টের শুকনো চকচকে মেঝের ওপর আধুনিক ঝকঝকে সাদা কমোড বসানো। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য সুইমিং পুল বানানো আছে, তার পাশে রাজকীয় পর্দাঝোলানো আরামকেদারা। পাশেই মাটির ঘরে পানীয় আর তোয়ালের সম্ভার।
সেদিক ছেড়ে এলাম রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপে। এখন এই আশ্বিনে মায়ের কাঠামোতে কুমোরশিল্পী নরম গঙ্গামাটিতে পা ডুবিয়ে আপন সৃষ্টিতে নিমগ্ন। আমাদের হাঁটাচলা, কথাবার্তায় ভ্রূক্ষেপহীন ওনার কাজ। কিছু ছবি তুলে মণ্ডপলাগোয়া দরদালানে ঘুরে বেড়ালাম।

আরও কত মহল, ছোটবাড়ি, ডাকবাংলো সবই একতলা। সেই অতিথিশালাগুলির চারপাশে ঘুরে আবার এসে উঠলাম মূলবাড়ির উঠোনে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতেই অন্য এক ধরনের শাড়ি পরা মহিলা আমাদের নমস্কার করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। লম্বা হলের একদিকে মন্ডল পরিবারের প্রাচীন পিয়ানো, তার ওপরের দেওয়ালে টাঙানো পরিবারের এক দম্পতির পুরোনো ছবি, নাম জানা গেল না।
একদিকের দেওয়ালে বটগাছের ঝুরিওলা প্রাচীন রাজবাড়ির ছবি দেখিয়ে সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট পরা এক কর্মী জানালেন এই অবস্থায় বাড়িটি কিনেছিলেন অজয় রাওলা।
সার দেওয়া চেয়ার টেবিলে তখন ন্যাপকিন, চামচ, মাটির সুদৃশ্য রেকাবি সাজানো। আমাদের ইচ্ছেমতো টেবিল বেছে নিতে বলা হল। মেয়ে একেবারে কোণে পিয়ানোর কাছের গদিওলা চেয়ার টেবিলে বসতে চাইল। আমাদের টেবিলের পাশেই কাঁচের দেওয়ালের ওপারে গোবিন্দ মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। একমাত্র এই মন্দিরেই আজও নিত্যপূজা হয়। বাকিগুলো সব ভেঙে পড়েছে। আরেকটি নির্মীয়মান মন্দির অবশ্য পথে আসতে চোখে পড়েছে।
এখানে খাবার ব্যবস্থা বেশির ভাগই থালি। আমাদের ছিল জমিনদারি ভেজ আর নন-ভেজ থালি। এছাড়া ক্লাসিক জমিনদারি থালি। প্রথমে তিনজনকেই মাটির থালায় গোল করে কাটা কলাপাতায় চূড়া করে ভাত, কুচি করা স্যালাড, বড়িগুঁড়ো ভাজা, ঝুরি আলুভাজা, বড়া ভাজা, আলুপোস্ত, মাটির সুন্দর ভাঁড়ে সোনা মুগের ডাল, সুক্তো এসব দিয়ে গেল। এরপর গলানো ঘি এসে পড়ল ভাতের ওপর। আরও আছে, রাজকীয় খাবার বলে কথা! একটা মাটির ভাঁড়ে তপসে ব্যাটার ফ্রাই, ভেজ থালির জন্য মোচার ঘন্ট, পনির পাতুরি। দুই আমিষ থালিতে কচুপাতা চিংড়ি, ভেটকি পাতুরি। পাশে রাখা মাটির রেকাবিতে এসে পড়ল গরম ফোলা ফোলা কড়াইশুঁটির কচুরি। এরপর এল ক্লাসিক জমিনদারি নন-ভেজ থালির জন্য চিকেন ডাক বাংলো আর জমিনদারি থালির জন্য মাটন কষা, সবার জন্য আমসত্ব খেজুরের চাটনি,পাঁপড়। পেটরোগা আমরা তিনজন এত খাবার কিভাবে খাব! অবশেষে ভাত, আলুভাজা, কচুপাতা চিংড়ি, বড়া ভাজা এসব সামান্য খেয়ে বাকিগুলো খাওয়া শুরু করলাম। প্রতিটি রান্নাই অসাধারণ হয়েছিল। সেই সঙ্গে বার বার মহিলা ও পুরুষকর্মীরা আরো কিছু লাগবে কিনা পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমাদের পেটের অবস্থা ততক্ষণে আইঢাই। এরপরে মিষ্টিমুখ, রসগোল্লা, সন্দেশ, মিষ্টি দই পান! কয়েক হাজার টাকা বিল মিটিয়ে মিষ্টি পান মুখে দিয়ে যখন ফেরার পথ ধরলাম সূর্য তখন মধ্যগগনে।

![]()

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায়-এর লেখালেখির প্রতি অদম্য ঝোঁক ছোটোবেলা থেকেই। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম - রঙমিলান্তি, করোনা, লক ডাউন ও আমার দেশ। স্মৃতিকথায় ভরা গদ্যগ্রন্থ - "অনুভবে পুরুলিয়া"। আনন্দবাজার পত্রিকাতে রবিবারের দক্ষিণবঙ্গ পৃষ্ঠায় ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হয়েছে।
![]()