 |
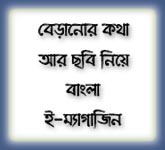 |
|
|
|
সেবাগ্রাম
অভিষেক রায়
সাল ১৯৩০। সবরমতী আশ্রম থেকে বেরিয়ে গান্ধীজি এক নতুন যাত্রা শুরু করলেন। এবার তাঁর পথ আরব সাগরের দিকে, ডান্ডিতে। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশের করা লবণ আইন। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের লবণ বানানো নিষিদ্ধ করেছিল। একমাত্র ব্রিটিশ সরকার তার নির্ধারিত জায়গায় বানাতে পারবে নুন এবং ভারতীয়দের দিতে হবে লবণ কেনার জন্য কর। মহাত্মা এই আইনকে রদ করার দাবিতে পথে নামলেন। এই আইন ভারতীয়দের বিরোধী। মানবাধিকার বিরোধী। এই যাত্রা 'লবণ সত্যাগ্রহ' বা 'ডাণ্ডি মার্চ' নামে ইতিহাস হয়ে আছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বিশাল সূচক ছিল এই পদযাত্রা। শুরু হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এক নতুন মোড় নিয়েছিল।
গান্ধীজির নিজের জীবনের পটভূমিকাও বদলে গিয়েছিল এরপরে। ১২ মার্চ ১৯৩০, তিনি সেই যে সবরমতী আশ্রম থেকে বেরোলেন, আর সেখানে ফেরা হয়নি। বলেছিলেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর ফিরবেন না এই আশ্রমে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে এই আশ্রম থেকেই সূচনা হয়েছিল তাঁর কর্মযজ্ঞ। চব্বিশ দিনের সেই পদযাত্রায় গান্ধীজি ২৪০ মাইল হাঁটলেন। গান্ধীজির এই হাঁটা পুরনো ফিল্মে ধরা আছে। এখনও ইউটিউবে দেখা যায়। প্রথমে আটাত্তর জন সহযোগী ছিলেন, তারপর দলে দলে লোক যোগ দিয়েছিল সেই পদযাত্রায়। ভিডিওতে দেখা যায় সরোজিনী নাইডুকে। লবণ সত্যাগ্রহে ব্রিটিশ শাসককে টলানো যায়নি। লবণ আইন প্রত্যাখ্যানও করানো যায়নি। তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তি তো দূরের কথা। ওই ভিডিও ক্লিপে এখনও দেখা যায় নির্মম পুলিশি লাঠিচার্জের ভয়াবহ দৃশ্য। পুলিশের লাঠির আঘাতের সামনে সত্যাগ্রহীরা আদর্শে অটল। মার খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে বা উঠে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু একজনও প্রত্যাক্রমণ করছে না। গান্ধীজি জানতেন ব্রিটিশ সরকারকে টলানো যাবে না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের কাছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের নিষ্ঠুর, নির্মম ও মানবতাবিরোধী দিকটা তুলে ধরা। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। অবশেষে ৬ এপ্রিল ডান্ডিতে সকাল সাড়ে আটটায় গান্ধী নুন হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে লবণ আইন ভাঙলেন। সারাদেশে মানুষ লবণ সত্যাগ্রহ পালন করল। "I want world sympathy in this battle of right against might" – সূচনা হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের। গান্ধীর এরপরের যাত্রা শুরু হল দক্ষিণে। ৪-৫ মে মধ্যরাতে গান্ধী ধারাসনায় গ্রেফতার হলেন। গান্ধীর গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে - সারা বিশ্বে। জেল থেকে মুক্তি পেলেন গান্ধী। কিন্তু এবার যাবেন কোথায়? কোথায় বানাবেন তাঁর কেন্দ্র? পরিব্রাজক তিনি বরাবরই। তিনি অনেকবারই হয়েছেন এমন গৃহহীন।
যমুনালাল বাজাজ এগিয়ে এলেন গান্ধীর সাহায্যে। দেশের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী যমুনালাল বাজাজ শুধু গান্ধীর অনুগামীই নন, তাঁকে বলা হত গান্ধীর পঞ্চম পুত্র। তৎকালীন সেন্ট্রাল প্রভিন্স-এর ওয়ার্ধায় তাঁর অতুল সম্পত্তি, জমি জায়গা। সেখানে তিনি আহ্বান করলেন গান্ধীকে। সবরমতী আশ্রম এবং গান্ধীর নাম সমার্থক হয়ে গেছে কিন্তু সবরমতী গান্ধীর একমাত্র আশ্রম নয়। গান্ধীজির আশ্রমজীবনের সূচনা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বসবাসকালে। ১৯০৪ সালে ডারবান শহরের কাছে সেই আশ্রমকে বলা হত ফিনিক্স সেটেলমেন্ট। এরপর ১৯১০-এ জোহানেসবার্গে তলস্তয় ফার্ম। ১৯১৫-য় গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছিলেন নিজভূমে। ভারতে তাঁর প্রথম আশ্রম কোচরবে। কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনেও কাটিয়েছেন। ১৯১৭-তে সবরমতী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা হল আশ্রম। ওয়ার্ধায় সেবাগ্রাম হল গান্ধীর শেষ আশ্রম। এই সেবাগ্রাম অচিরেই হয়ে উঠল তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক সাক্ষী এই আশ্রম যা বহু মানুষ এখনও জানে না।

২০২১ সালে আমি প্রথম সেবাগ্রামে আসি। সেইসময় দিল্লীতে সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলন চলছে। তাতে কয়েকদিনের জন্যে যোগ দিতে যাওয়ার আগে কিছু রাজনৈতিক সহযোগীদের সঙ্গে এসেছিলাম এখানে। আমি কলকাতা থেকে বাকিরা মুম্বাই থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, বিকল্প শিক্ষা, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন এবং বিশেষ করে গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই তিন দিনে সেবাগ্রাম আশ্রমের একটি চমৎকার দিক দেখেছিলাম, সকালে খোলা এবং সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ে বন্ধ হওয়া ছাড়া বাকি সময়ে সকলের জন্যে আশ্রমে অবারিত দ্বার। সারা বছর আশ্রমে চলে নানান কর্মশালা। জাতীয়স্তরের বিভিন্ন সংগঠন সেবাগ্রামকে বেছে নেয় তাদের শিবির হিসেবে। গতবছর যখন গেলাম, তখনও দেখলাম দুটি শিবির চলছে। গান্ধী আশ্রম ছাড়াও সেবাগ্রাম খাদি বস্ত্র, কুটিরশিল্প এবং গ্রামীণ সংস্কারমূলককাজের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। যমুনালাল বাজাজ গান্ধীজি আসার কিছুকাল আগে থেকেই ওয়ার্ধায়, তাঁর নিজের গৃহ থেকেই গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শুরু করেছিলেন গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ বিষয়ককাজ। শুরু হয়েছিল খাদি বস্ত্র নির্মাণকেন্দ্র। ১৯২০-র দশক থেকেই গান্ধীর অন্যতম প্রধান শিষ্য বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধার কাছেই পৌনারে শুরু করেছেন তাঁর আশ্রম।
গান্ধী প্রথমে এসে উঠলেন যমুনালাল বাজারের গৃহে। এই জায়গার নাম কিন্তু সেবাগ্রাম নয়। জেনে নেওয়া যাক এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ওয়ার্ধা শহর থেকে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে সেগাঁও গ্রাম। যমুনালাল বাজাজ সেই গ্রামের প্রধান 'মালগুজার', প্রায় জমিদার বলা যায়। ইংল্যান্ড থেকে গান্ধীজির সত্যাগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়ে ম্যাডিলিন স্লেইড এসে পড়েছেন ভারতে প্রায় এক দশক আগে। তাঁর ভারতীয় নাম হয়েছে মীরাবেন। গান্ধীজির নির্দেশে তিনিও ভারতে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে, সেগাঁওতে এসে শুরু করেছেন তাঁর কাজ। সেখানে একটি পর্ণকুটির বানিয়ে অতি সামান্য আয়োজনে তিনি তখন বসবাস করছেন। যমুনালাল বাজাজের গৃহ থেকে গান্ধীজি ৩০ এপ্রিল ১৯৩৪-এ সেগাঁওয়ে এসে পৌঁছলেন। মীরাবেন গান্ধীর আসার খবর পেয়েই একটি ছোট কুটিরের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। বাঁশের ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। মেঝেতে মাদুর। পেয়ারা গাছের তলায় পর্দা দিয়ে একটি স্নানের জায়গা। গাছের ছায়ায় তৈরি করে দিয়েছেন তাঁর একটি অফিস, যেখানে গান্ধী লিখবেন তাঁর চিঠি, সম্পাদনা করবেন 'হরিজন' পত্রিকা। সেদিন বিকেলে গান্ধী একটি প্রার্থনা সভায় গ্রামবাসীদের কাছে জানান 'আমি আপনাদের সেবা করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে আমার প্রতি অবিশ্বাস ও ভীতি থাকতেই পারে কারণ আমার প্রধান লক্ষ্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। আমি ব্রাহ্মণ ও চামারকে এক মনে করি এবং জন্মগতভাবে উচ্চ, নীচ বিচার করাকে পাপ ভাবি। কিন্তু আমি আমার মতামত আপনাদের ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেব না। আমি বিষয়টি আলোচনা, তর্ক এবং উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করবো। আমি অসুস্থকে সাহায্য করব এবং সকলকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে, গ্রামকে পরিষ্কার রাখতে, এবং কুটির শিল্পকে পুনরূজ্জীবিত করতে উৎসাহিত করব। আমি আশা রাখব এবং খুশী হব যদি আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন।' সেবাগ্রামে খুঁটি বাঁধলেন গান্ধী। তাঁর গ্রামস্বরাজ ভাবনার বাস্তবিক প্রতিফলিতরূপ গান্ধী এখানেই প্রয়োগ করার অবকাশ পান। সে কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু সহযোগী।

সেগাঁও জায়গাটি কেমন ছিল? গান্ধীর এই কর্মযজ্ঞের এক অন্যতমা আশা দেবী আর্যনায়কমের লেখায় জানা যায় তৎকালীন সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরারের সাতশো মানুষের একটি গ্রাম ছিল সেগাঁও। বছরের কিছু সময়ে বৃষ্টির জন্যে সবুজ থাকলেও বাকী সময় রুক্ষ মাটি ও ধুলোয় ভরা ছিল গ্রাম। জলকষ্ট ছিল তীব্র। জাত বিশেষে কুয়োর জল অতি সাবধানতায় সংরক্ষিত হত। বিহারের চাম্পারন থেকে কাজ শুরু করেছিলেন গান্ধী। চ্যালেঞ্জ তুলে নেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। সেগাঁও যেন গান্ধীর কর্মক্ষেত্র হওয়ার জন্যে তৈরিই ছিল। সেগাঁও থেকে সেবাগ্রাম নামকরণের ইতিহাসটাও জেনে নেওয়া যাক। মুম্বাই- নাগপুর রুটে খান্দেশ অঞ্চলে একটি জায়গার নাম শিগাঁও। গান্ধী এখানে বসবাস শুরু করার পরে তাঁকে লেখা সব চিঠি ডাকবিভাগ পাঠিয়ে দিচ্ছিল সেই জায়গায়। তখন এই জায়গাটির নাম পরিবর্তন করে 'সেবাগ্রাম' করে দেওয়া হয়। হাওড়া- মুম্বাই ট্রেনরুটে ওয়ার্ধায় লুকিয়ে আছে দেশের এতো এক ঐতিহ্যশালী ইতিহাস। নাগপুরের পরের জাংশন - মুম্বাই, পুনেগামী ট্রেন ওয়ার্ধায় থামে। উন্নয়নের জোরে যখন গ্রাম, মফস্বল, টাউন সব শহরে পরিণত হচ্ছে, তখন কয়েকদিন ওয়ার্ধায় একটি প্রভিন্সিয়াল টাউনের স্বাদ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশত বিধ্বংসী উন্নয়নের প্রবেশ ঘটেনি এখানে। স্টেশন থেকে সেবাগ্রাম আশ্রম ৮ কিলোমিটার পথ। ইচ্ছে হলে ওয়ার্ধা শহরে থাকতে পারেন কিন্তু যদি নিরিবিলি, শান্ত আশ্রম এলাকার পরিবেশে সাধারণ থাকতে চান তবে, সেবাগ্রামের বিপরীতে যাত্রীনিবাস আদর্শ স্থান।
ওয়ার্ধা থেকে গান্ধী যখন সেগাঁওয়ে চলে এলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন এখানেই থাকবেন এবং এখান থেকেই শুরু করবেন তাঁর কাজ, যমুনালাল বাজাজ সেখানে তাঁর বসবাসযোগ্য গৃহনির্মাণে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু গান্ধীর কড়া নির্দেশ ছিল যে গৃহ নির্মাণে একশো টাকার বেশি খরচ করা যাবে না। এই নিরাভরণ, অতি সাধারণ আশ্রমের মাটিতে গাঁথা আছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস। সত্যিই কি চমক লাগেনা, যখন শুনি এখানেই ১৪ জুলাই ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মিটিংয়ে বসেছিলেন সব জাতীয় নেতা। তার কয়েক বছর আগে ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে যখন খুব জটিল পরিস্থিতি চলছে, সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু গান্ধীজি তাঁর পদ মনোনীত করেননি। সংকট কাটাতে সুভাষ বসু, গান্ধীজির সাথে এই সেবাগ্রামেই মিটিং করতে এলেন। এই নিস্তরঙ্গ স্থানটি দেখলে কে বলবে, পরাধীন ভারতের প্রায় দেড় দশক এখান থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এখানকার কুটির, প্রতিটা গাছ যেন তার সাক্ষী। অথচ কী সাধারণ।

সেবাগ্রাম আশ্রমে এলাকা জুড়ে বিভিন্ন কুঠি। আদি নিবাস, বাপু কুঠি, বা কুঠি, গান্ধীর শেষ নিবাস যা লাস্ট রেসিডেন্স নামে পরিচিত। প্রথমে আদি নিবাসেই গান্ধী, তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা ও অন্য সহযোগীদের সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু এতগুলো মানুষের সঙ্গে থাকতে বৃদ্ধ বয়সে কস্তুরবাজীর স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যা হচ্ছিল। গান্ধীজির আপত্তি সত্ত্বেও যমুনালাল বাজাজ একটি স্বতন্ত্র কুটির তৈরি করে দেন। সেই কুটিরের নাম 'বা কুঠি'। কস্তুরবা ছিলেন সকলের 'বা' অর্থাৎ জননী।
 গান্ধীর কুটিরে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত জিনিস। সেখানে রয়েছে সেই বিখ্যাত তিনটে বানরের মূর্তি। মাটির কুটির কিন্তু আমোদ পেতে হয়, গান্ধীর শৌচাগার দেখে। অত্যন্ত আধুনিক ও আরামপ্রদ। আরেকটি ছোটোঘরে একটি কাঠের তক্তা যেখানে গান্ধী স্নানের পূর্বে তৈলমর্দন করতেন।
গান্ধীর কুটিরে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত জিনিস। সেখানে রয়েছে সেই বিখ্যাত তিনটে বানরের মূর্তি। মাটির কুটির কিন্তু আমোদ পেতে হয়, গান্ধীর শৌচাগার দেখে। অত্যন্ত আধুনিক ও আরামপ্রদ। আরেকটি ছোটোঘরে একটি কাঠের তক্তা যেখানে গান্ধী স্নানের পূর্বে তৈলমর্দন করতেন।
তুলনায় কস্তুরবার কুটির বড় অপ্রশস্থ। মনে পড়ে যেতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে মা সারদামণির ঘরের কথা। বা-কুঠিতে কাঁচের বাক্সে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত শাড়ি, জ্যাকেট। এই অনন্যসাধারণ নারী, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী হয়ে থেকেছেন আজীবন। কিন্তু তাঁর নিজের কথা কোথাও লিখে যাননি। এখানে একটা ফলক দেখে বেশ চমকে যেতে হয়। আত্মজীবনীতে গান্ধী লিখেছিলেন, 'প্যাসিভ রেজিস্টেন্স' প্রথম শিখেছিলেন স্ত্রীর থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন একরাতে দুজনের বচসার পরে তিনি যখন স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন, সেই সময় কস্তুরবার নীরব প্রতিরোধ তাঁর জীবনে চরম উপলব্ধি এনেছিল। এখানে একটা ফলক দেখে বেশ চমকে যেতে হয়। ১৯০৮ সালে ৯ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁর কারাবাস হয়, তখন সেখান থেকে সহধর্মিনীকে লেখা একটি মর্মস্পর্শী পত্র।
আশ্রমের আরেকদিক হল নঈ তালিম স্কুলের অংশ। গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটেছিল এই আশ্রমে। নঈ তালিম স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন আশা অধিকারী ও তাঁর সিংহলি স্বামী এডওয়ার্ড উইলিয়ামস আর্যনায়কম। গান্ধীজি যখন তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা পরীক্ষা করার কথা ভাবলেন তখন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন উপযুক্ত কাউকে সেবাগ্রামে পাঠাতে। রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন আশা দেবী ও ই.ডব্লিউ. আর্যনায়কমকে। আশা দেবী ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা, লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের দিদি।
 আর্যনায়কম ছিলেন শ্রীলঙ্কার জাফনা অঞ্চলের বাসিন্দা। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন ছাত্র, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দুজনেই বাকী জীবনটা কাটিয়েছিলেন সেবাগ্রামে। নঈতালিম কুটিরের বাইরে ফলকে লেখা আছে দুজনের সেবাগ্রামে যোগ দেওয়ার ইতিহাসে কথা। রয়েছে আশা দেবী ও আর্যনায়কমের ছবি, মাটিতে তাঁদের বসার ডেস্ক। আর্যনায়কম ছুটিতে নিজদেশ জাফনায় গিয়ে মারা যান ১৯৬৭ সালে। আশা দেবী ১৯৭০-এ। এরপরে কিছুকাল চলার পরে নইতালিম স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় তিন দশক বাদে ২০০৩-এ আশা দেবীর শতবর্ষে আবার সেই স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন স্কুলের নাম আনন্দবন।পরিপূর্ণ নঈ তালিম পদ্ধতিতে স্কুল এখন চলে না। বাস্তবিকভাবে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু পদ্ধতির কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল হাতের কাজের জিনিস বানানো। এ ব্যতীত প্রকৃতিপাঠ এবং কৃষি। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা ধানের গাছ লাগায়। পরিচর্যা করে। শিশুদের হাতের কাজের জিনিস এবং শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নিষ্ঠা বেশ মুগ্ধ করার মতো। এখানে যান্ত্রিক নিয়মে কিছু চলে না। টালির ঘরের স্কুল। বেল বাজে না। পড়ে ঘন্টা। কিন্তু একটি নির্মল আনন্দঘন পরিবেশ। বিকল্প শিক্ষা বিষয়ে যারা হাতে কলমে কাজ করছেন বা গবেষণা করেছেন, সেইসব উৎসাহী মানুষেরা এখানে এসে থাকেন। এখানে কয়েকটি অতিথিশালা রয়েছে। রয়েছে একটি কিচেন। সাধারণ মারাঠি রান্না। ভাত, রুটি, দুরকমের ডাল, একটি সবজি, রায়তা। সকলকেই থালা নিয়ে মাটিতে আসনে বসে খেয়ে, আবার বাসন ধুয়ে রাখতে হয়। এখানে এলে, দেখা হবে সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে। আসেন কৃষি ও বস্ত্রশিল্পের কর্মীরাও। আশ্রমে রয়েছে পারচুরে কুঠি। সংস্কৃত পণ্ডিত পারচুরে শাস্ত্রী সেবাগ্রামে এসে ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়। কুষ্ঠরোগীদের বিষয়ে সেই সময়ে মানুষের মনে ভয়ঙ্কর ভীতি, ঘৃণা কাজ করত। তাদের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষত না। গান্ধী নিজে পারচুরে শাস্ত্রীর সেবা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। এর মাধ্যমে কুষ্ঠরোগীদের প্রতি মানুষের ঘৃণার ভাব গান্ধী দূর করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে গান্ধীর নির্দেশে সংস্কৃতজ্ঞ পারচুরে শাস্ত্রী আশ্রমিকদের বিবাহে পৌরহিত্য করতেন।
আর্যনায়কম ছিলেন শ্রীলঙ্কার জাফনা অঞ্চলের বাসিন্দা। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন ছাত্র, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দুজনেই বাকী জীবনটা কাটিয়েছিলেন সেবাগ্রামে। নঈতালিম কুটিরের বাইরে ফলকে লেখা আছে দুজনের সেবাগ্রামে যোগ দেওয়ার ইতিহাসে কথা। রয়েছে আশা দেবী ও আর্যনায়কমের ছবি, মাটিতে তাঁদের বসার ডেস্ক। আর্যনায়কম ছুটিতে নিজদেশ জাফনায় গিয়ে মারা যান ১৯৬৭ সালে। আশা দেবী ১৯৭০-এ। এরপরে কিছুকাল চলার পরে নইতালিম স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় তিন দশক বাদে ২০০৩-এ আশা দেবীর শতবর্ষে আবার সেই স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন স্কুলের নাম আনন্দবন।পরিপূর্ণ নঈ তালিম পদ্ধতিতে স্কুল এখন চলে না। বাস্তবিকভাবে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু পদ্ধতির কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল হাতের কাজের জিনিস বানানো। এ ব্যতীত প্রকৃতিপাঠ এবং কৃষি। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা ধানের গাছ লাগায়। পরিচর্যা করে। শিশুদের হাতের কাজের জিনিস এবং শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নিষ্ঠা বেশ মুগ্ধ করার মতো। এখানে যান্ত্রিক নিয়মে কিছু চলে না। টালির ঘরের স্কুল। বেল বাজে না। পড়ে ঘন্টা। কিন্তু একটি নির্মল আনন্দঘন পরিবেশ। বিকল্প শিক্ষা বিষয়ে যারা হাতে কলমে কাজ করছেন বা গবেষণা করেছেন, সেইসব উৎসাহী মানুষেরা এখানে এসে থাকেন। এখানে কয়েকটি অতিথিশালা রয়েছে। রয়েছে একটি কিচেন। সাধারণ মারাঠি রান্না। ভাত, রুটি, দুরকমের ডাল, একটি সবজি, রায়তা। সকলকেই থালা নিয়ে মাটিতে আসনে বসে খেয়ে, আবার বাসন ধুয়ে রাখতে হয়। এখানে এলে, দেখা হবে সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে। আসেন কৃষি ও বস্ত্রশিল্পের কর্মীরাও। আশ্রমে রয়েছে পারচুরে কুঠি। সংস্কৃত পণ্ডিত পারচুরে শাস্ত্রী সেবাগ্রামে এসে ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়। কুষ্ঠরোগীদের বিষয়ে সেই সময়ে মানুষের মনে ভয়ঙ্কর ভীতি, ঘৃণা কাজ করত। তাদের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষত না। গান্ধী নিজে পারচুরে শাস্ত্রীর সেবা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। এর মাধ্যমে কুষ্ঠরোগীদের প্রতি মানুষের ঘৃণার ভাব গান্ধী দূর করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে গান্ধীর নির্দেশে সংস্কৃতজ্ঞ পারচুরে শাস্ত্রী আশ্রমিকদের বিবাহে পৌরহিত্য করতেন।

৮ অগস্ট ১৯৪২ বোম্বাই শহরে (বর্তমান মুম্বাই) গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে (বর্তমান অগাস্ট ক্রান্তি ময়দান) গান্ধীর ডাকে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এ যেভাবে গর্জে ওঠে সারা ভারত, তার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৪ জুলাই ১৯৪২ সালে সেবাগ্রামে বাপু কুঠিতে। সেইদিনই গান্ধীসহ সমস্ত নেতা, নেত্রীদের গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকার। গান্ধীর স্থান হয় পুনের আগা খান প্যালেসে। সাথে কস্তুরবা, মহাদেব দেশাই, সরোজিনী নাইডু, সুশীলা নায়ার এবং অন্যান্যরা। বন্দী অবস্থাতেই আগা খান প্যালাসে মৃত্যু হয় মহাদেব দেশাইয়ের ১৯৪২-এর ১৫ অগস্ট এবং কস্তুরবা গান্ধীর ১৯৪৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি। তাঁদের আর ফেরা হয়নি সেবাগ্রামে। ১৯৪৪-এ মুক্তি পাওয়ার পরে গান্ধী অবশ্য সেবাগ্রামে ফেরেন। ১৯৪৬-এর অগাস্টে নোয়াখালিতে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হল। গান্ধী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নোয়াখালি যাবেন। ২৬ অগস্ট তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আর ফিরে আসেননি তাঁর সেবাগ্রামে।

ওয়ার্ধায় রয়েছে মগন সংগ্রহালয়। এটি স্টেশনের কাছেই। গান্ধীর অহিংস নীতি ও আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন মগনলাল গান্ধী, সম্পর্কে গান্ধীজির তুতো ভাই। 'সত্যাগ্রহ' নামটি তাঁরই দেওয়া। গান্ধী যখন 'চরকা'কে জাতীয় প্রতীক করলেন এবং চাইলেন ঘরে ঘরে সবাই চরকায় সুতো কাটুক, সেই সময় মগনলাল গান্ধী খাদি প্রসারে খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সংগ্রহালয়ে রয়েছে কয়েকশো রকমের চরকা।

পাশেই মগন খাদির কর্মশালা। তুলো থেকে সুতো, সুতো থেকে তাঁতে বস্ত্র এবং তারপর কাপড় রাঙানো, ব্লক প্রিন্ট এই পুরোটাই সেখানে দেখা যায়। সেবাগ্রামেও রয়েছে এইরকম একটি বড় ইউনিট। সেবাগ্রাম থেকে ৬ কিলোমিটারের মধ্যে পওনারে আছে বিনোবা ভাবের আশ্রম। গান্ধী আসার এক দশক আগেই তিনি এখানে এসে শুরু করেছিলেন সমাজসেবার কাজ। ১৯৫১তে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের সূচনা করেন। ওয়ার্ধা শহরে রয়েছে গান্ধী জ্ঞান মন্দির লাইব্রেরি। বইয়ের সমৃদ্ধ সংগ্রহ। তার উল্টোদিকেই যমুনালাল বাজারের বাসভবন 'বাজাজ ভবন'। ত্রিশ, চল্লিশের দশকে বরেণ্য সব নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, খান আব্দুল গফুর খান, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু যখনই কেউ সেবাগ্রামে এসেছেন, তখন এই বাসভবনে থেকেছেন। হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। তবে এই বাসভবন এখনও বাজাজ পরিবারের ব্যক্তিগত মালিকয়ানায়। সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। সাত কিলোমিটারের মধ্যে আরেকটি দ্রষ্টব্য জায়গা রয়েছে গ্রামসেবা মণ্ডল। এটিও বিনোভা ভাবের নির্মাণ। ১৯৩৮ সালে স্থানীয় গ্রামীণ নারীদের কর্মোপযোগী করে তুলতে এই প্রয়াস। এখানে রয়েছে খাদি কেন্দ্র। একদম জৈব পদ্ধতিতে তৈরি হয় সুতো। বিভিন্ন আকারের চরকা নির্মিত হয় এখানে। চাইলে কিনতেও পারা যায় চরকা। রয়েছে তেলের ঘানি। তৈরি হয় বিশুদ্ধ সর্ষের তেল। সেবাগ্রামের পরে গ্রামসেবাও গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ওয়ার্ধায় আছে বিশ্ব শান্তি স্তূপ। সেই আকর্ষণীয় শ্বেত স্থাপত্য দেখবার মতো।
শেষ করব নিজস্ব ভালো লাগার একটি অভিজ্ঞতা দিয়ে। তা হলে সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রার্থনা। বাপু কুটিরের সামনে গান্ধীর নিজের হাতে লাগানো একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে রোজ প্রার্থনা হয়। ভোর ও সন্ধ্যা পাঁচটায়। কস্তুরবাজীর কুটির যার নাম 'বা কুঠি' -র সংলগ্ন স্থানে। উল্টোদিকেই গান্ধীজির 'বাপু কুঠি'। সামনে গান্ধীর পোঁতা একটি অশ্বত্থ গাছ। নীচে রাখা থাকে গান্ধীর ব্যবহৃত কাঠের পিঁড়ি। সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রার্থনার পরে গান্ধীর লেখা কোনও গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ হয়। কখনো গান্ধীর পছন্দের রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলা থেকে দূরে, বেরার অঞ্চলে এসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে কোন বাঙালির না ভালো লাগে! সে সুর যাই হোক। হয় গান্ধীর প্রিয় ভজন। খুবই নিরাভরণ আয়োজন। এই প্রার্থনা আমার মন ভরিয়ে দিত। রোজ অপেক্ষা করে থাকতাম, এই সময়টার জন্যে। মনে পড়ে ২০২১-এ এই প্রার্থনার সময়ে দূর থেকে আজানের সুর খুব হালকাভাবে ভেসে এসেছিল। মুহূর্তে শিহরণ জাগে। এই প্রার্থনা দেখে আমার ভিতর থেকে দুটি বাক্য বেরিয়ে আসে ' বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ' । সকল মানবজাতির মঙ্গল কামনার জন্যে এই প্রার্থনা। এই সময়টায় তাই পেয়েছিলাম এক অন্য পরিবেশ ও অনুভূতি। যা ভোলার নয়।

![]()

অভিষেক রায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছেন দেশে, বিদেশে। বর্তমানে স্বাধীন গবেষক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। লেখালেখি করতে ভালবাসেন উনিশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনী, পরিবেশ এবং অবশ্যই ভ্রমণ বিষয়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বেড়ান। ব্যক্তিগত স্তরে পরিবেশ, সামাজিক ও মানবাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়।
![]()