 |
 |
|
|
|
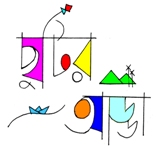
বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com
রহস্যময় আন্ধারমানিক
জিয়াউল হক শোভন
রনি ভাইয়ের ফোন পেয়েই চলে গেলাম তার বাসায়। গুগল ম্যাপে সে আমাকে দেখাল এক আশ্চর্য যায়গা, যার নাম লেখা "দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট", বান্দরবানের গহিন অঞ্চলে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের সীমান্তে এর অবস্থান। ব্যাস, নড়েচড়ে বসলাম আমরা। একটু খোঁজখবর করতেই পেয়ে গেলাম "দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট" ওরফে "আন্ধারমানিক" সম্পর্কে তথ্য।
 ২০০৮ সালে ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর-এর সদস্যরা এই জায়গায় একটি অভিযান চালায়। সেটি ছিল বাংলাদেশেই উৎপত্তি হয়েছে এমন একমাত্র নদী, সাঙ্গুর উৎস সন্ধানের একটি অভিযান। পরবর্তীতে তারা এই অঞ্চল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের উন্মোচন করে। এই সার্থক অভিযানে তাঁরা উপভোগ করে গহিন সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এবং আন্ধারমানিকের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
প্রধানত তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের উপর নির্ভর করে ২০১১ সালের অক্টোবরে আমরা তিনজন - আমি, সম্রাট ভাই এবং রনি ভাই রওনা দিয়েছিলাম আন্ধারমানিকের উদ্দেশ্যে।
২০০৮ সালে ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর-এর সদস্যরা এই জায়গায় একটি অভিযান চালায়। সেটি ছিল বাংলাদেশেই উৎপত্তি হয়েছে এমন একমাত্র নদী, সাঙ্গুর উৎস সন্ধানের একটি অভিযান। পরবর্তীতে তারা এই অঞ্চল সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের উন্মোচন করে। এই সার্থক অভিযানে তাঁরা উপভোগ করে গহিন সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এবং আন্ধারমানিকের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
প্রধানত তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের উপর নির্ভর করে ২০১১ সালের অক্টোবরে আমরা তিনজন - আমি, সম্রাট ভাই এবং রনি ভাই রওনা দিয়েছিলাম আন্ধারমানিকের উদ্দেশ্যে।
ঢাকা থেকে রাতের বাসে করে বান্দরবান, অতঃপর পরদিন বান্দরবান শহর থেকে লোকাল বাসে করে থানচি। সেখান থেকে গাইড হিসেবে আমাদের সাথে যাওয়ার কথা অভিজ্ঞ গাইড অং সাইয়ের। কিন্তু সে অসুস্থ থাকায় লোকাল গাইড লালমুন বম এবং দুই জন মাঝি সহ নৌকা ভাড়া করে আমরা রওনা দিলাম তিন্দুর উদ্দেশ্যে। গাইড এবং মাঝি সহ নৌকায় আমরা মোট পাঁচজন, সাথে ব্যাকপ্যাক এবং অন্যান্য সারঞ্জাম। পদ্ম ঝিরির মুখে এসে আমাদের নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হল। শেষমেশ সন্ধ্যার দিকে নিরাপদেই আমরা তিন্দু পৌঁছাই। সাঙ্গুর ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে সারাদিনের ক্লান্তি চলে গেল। পাথর দিয়ে চুলা বানিয়ে সাথে করে নিয়ে আসা চাল, ডাল, তেল এবং মশলা সহযোগে আমরা খিচুড়ি রান্না করতে বসে গেলাম। রাতে তাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে সাঙ্গুর পাড়েই আমাদের তাঁবু ফেললাম। ঠিক হল গাইড সহ নৌকার মাঝিরা নৌকাতেই ঘুমাবে। 
সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। নিছক শখের বসেই আমরা জ্যোৎস্নার আলোয় তিন্দু ঝিরি ধরে হাঁটা শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অজান্তেই অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ি ঝিরি আর এর সাথে পিচ্ছিল পাথরে কতবার যে পড়েছিলাম, তার ঠিক নেই। তারপরও রোখ চেপে গিয়েছিল এই ঝিরির শেষ দেখে ছাড়ব। জ্যোৎস্নার আলোয় টর্চ লাইটের অভাবও আমরা বোধ করছিলাম না। একটা সময় ক্লান্ত হয়ে এবং পরদিন ভোরে ওঠার কথা মনে পড়ায় ফিরতি পথ ধরলাম। আসলে তিন্দুতে বর্তমানে অনেক পর্যটকরা গেলেও তিন্দু ঝিরির সৌন্দর্যের কথা অনেকেই জানেননা।
পরদিন ভোরে মোরগের প্রথম ডাকেই আমাদের ঘুম ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে আগেরদিনের খিচুড়ির অবশিষ্টাংশ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম বড় মদকের উদ্দেশ্যে। পথে বড়পাথর নামক অঞ্চলে বিশাল বিশাল পাথরের মাঝখানে নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে লগি দিয়ে ঠেলে এবং বৈঠা বেয়ে খুব সাবধানে এগোতে হয়। এখানে রয়েছে প্রচুর ডুবোপাথর, যার সামান্য আঘাতেই নৌকা তলিয়ে যেতে পারে। সাঙ্গু নদীর আশি শতাংশ দুর্ঘটনাই এই অঞ্চলে হয়। নিরাপদে বড়পাথর পার হয়ে রেমাক্রি ছাড়িয়ে আমাদের নৌকা চলল বড় মদকের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ি নদীর প্রচণ্ড উজান স্রোত উপেক্ষা করে আমরা বড় মদক পৌঁছলাম। এখানে রয়েছে বেশ বড় একটি বিজিবি ক্যাম্প। সময়ের স্বল্পতায় বড় মদকে না থেমে আমরা এগিয়ে গেলাম আন্ধারমানিকের উদ্দেশ্যে। স্থানীয় ভাবে এটি "মুরং ওয়া" নামে পরিচিত। এখানে একটি পাড়া আছে যার নাম মুরং ওয়া পাড়া। বড় মদক থেকে নদীপথে এই পাড়ার দূরত্ব আট কিমি। এর পরেই শুরু হবে রহস্যময় সৌন্দর্যের জগৎ আন্ধারমানিক।
 ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর এর সদস্যদের ভাষায় বলতে গেলে, "দীর্ঘ এই নদীপথের দুই পাশের পাহাড়ের দেয়াল খাড়া নেমে গেছে পানির গভীর তল পর্যন্ত। পাহাড়ের উঁচু উঁচু গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছায় খুব কম। তাই এই জায়গার নাম আন্ধারমানিক। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বয়ে চলেছে অসংখ্য ঝরনা"।
ডি-ওয়ে এক্সপেডিটর এর সদস্যদের ভাষায় বলতে গেলে, "দীর্ঘ এই নদীপথের দুই পাশের পাহাড়ের দেয়াল খাড়া নেমে গেছে পানির গভীর তল পর্যন্ত। পাহাড়ের উঁচু উঁচু গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছায় খুব কম। তাই এই জায়গার নাম আন্ধারমানিক। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বয়ে চলেছে অসংখ্য ঝরনা"।
সেইরকম একটি ঝরনার কাছে এসে আমাদের নৌকা থামালাম। এখান থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা হলো এবং ঝরনায় গোসল করে আমরা শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করলাম। ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছিলাম আন্ধারমানিকের অন্ধকার জগৎ নদীপথে সামনে এগিয়ে গেছে। এই রাস্তা লিক্রি পর্যন্ত গেছে। সেখান থেকে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের সীমানা কাছেই। আমাদের ইচ্ছা ছিল লিক্রি পর্যন্ত পৌঁছে সাঙ্গু রিজার্ভ ফরেস্ট এবং সাঙ্গুর উৎস খ্যাত পানছড়া ঝিরি দেখে আসব। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত এখানে একটি হাতির ট্রেইল আছে।
কিন্তু এখানেই বাঁধল বিপত্তি, কোন এক অজানা কারণে আমাদের গাইড এবং তার সাথে নৌকার দুই মাঝি আর সামনে এগোতে রাজি হলো না। তাদেরকে আমরা যতই বোঝাই এবং টাকা পয়সা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলি, কিন্তু কিছুতেই তারা আর সামনে এগোবে না। এদিকে নৌকা ছাড়া এই পথে এগোনো অসম্ভব। শেষে বাধ্য হয়েই আন্ধারমানিকের রহস্যময় অন্ধকারকে পিছনে ফেলে আমাদেরকে ফিরে আসতে হলো। দূর্বার ভাবে সেই পথ আমাদেরকে টানছিল আরও ভিতরে যাওয়ার, কিন্তু কিছু করার নেই। অং সাইয়ের কথা খুব মনে পড়ল, সে থাকলে হয়তো এই পরিস্থিতি হতো না, আমরা আরও ভিতরে যেতে পারতাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আবার আসব এখানে, এই অন্ধকার জগতের শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু আজ দু' বছর হতে চললো, সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় এখনও যাওয়া হলো না। সেই ব্যর্থ অভিযানের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে।


ভ্রমণপ্রেমী জিয়াউলের স্বপ্ন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

|
![]()
মন্দির-নগরীতে কিছুক্ষণ
রিমি মুৎসুদ্দি
আলেক্স রাদারফোরড আর উইলিয়াম ডালরিম্পল পড়ে ইতিহাসে মজেছিলাম। কিন্তু মুঘল স্মৃতির ছোঁয়া পেতে গেলে ছুটে যেতে হবে দিল্লি-আগ্রা। সেতো সময়ের ব্যাপার। এদিকে হপ্তাহান্তের এক ছুটিতে হঠাৎই জেগে উঠল ভ্রমণ পিপাসা। ইতিমধ্যে হাতে এসেছে অভয়পদ মল্লিকের "বিষ্ণুপুরের ইতিহাস-পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীন সাম্রাজ্য"। আনুমানিক ৬৯৫ বঙ্গাব্দে রাজা আদিমল বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩০০ বছর পরে মল্ল রাজা জগ্যমল্ল বিষ্ণুপুরের প্রচলিত মা মৃন্ময়ীদেবীর ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজধানী স্থাপন করেন। এইসব পড়তে পড়তে মনে হল হাতের কাছেইতো বিষ্ণুপুর... ঘুরেই আসি।
রাজা বীরভদ্র ছিলেন মল্ল রাজবংশের শ্রেষ্ঠতম রাজা। তিনি মুঘলদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন এবং আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদের পাশে ছিলেন। বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে এসে বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরপর তিনি বিষ্ণুপুরকে বৈষ্ণব ধর্ম ও স্থাপত্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে বীর হাম্বীর, বীরসিংহ প্রমুখ মল্লরাজাদের আমলে প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর। বীরভদ্র এবং অন্যান্য মল্ল রাজাদের কল্যাণে বিষ্ণুপুর আজ 'পশ্চিমবঙ্গের মন্দির নগরী'। ল্যাটেরাইট অথবা ইঁটের উপর টেরাকোটার কাজ করা এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি এক অভূতপূর্ব ভারতীয় স্থাপত্যকলার সাক্ষী। যে স্থাপত্যরীতি বিষ্ণুপুরে সবচেয়ে সমাদৃত তাকে একবর্তনী শৈলী বলা হয়। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত দেওয়াল ও ইষৎ ঢালু ছাদের কেন্দ্রে একটিমাত্র চূড়ার বিন্যাস এই রীতির বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুপুরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সংখ্যা তিরিশের নীচে হবে না। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি দেউল, চালা, রত্ন প্রভৃতি স্থাপত্যগত দিক থেকে পৃথক পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে বিখ্যাত জোড়বাংলা মন্দির। মল্লেশ্বর, মদনমোহন, জোড়বাংলা, মুরলীমোহন, শ্যামরায় মন্দিরগুলি ইঁটের তৈরি। কালাচাঁদ, লালজী, মদনগোপাল, রাধামাধব, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, নন্দলাল মন্দিরগুলি ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। মন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যে ফুটে উঠেছে দেব-দেবী, সমাজজীবন, ফুল-লতা-পাতা,পশুপাখির নানান মোটিফ। শুধু অসাধারণ স্থাপত্যই নয়, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতজগতে যে বিশিষ্ট ঘরানার একদা সৃষ্টি হয়েছিল তার ধারা আজো অম্লান। সঙ্গীতাচার্য যদুভট্টের জন্মস্থানও এই বিষ্ণুপুর।
দুর্গাপুর থেকে গাড়িতে আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভ করে পৌঁছে গেলাম 'পশ্চিমবঙ্গের মন্দির নগরী' বিষ্ণুপুরে (কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে করেও যাওয়া যায়। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, আরণ্যক এক্সপ্রেস-এই ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে ছাড়ে। ট্রেনে সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা)। একজন গাইড ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা। পাঁচ টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র কিনতে হল। এতে রাসমঞ্চ, জোড়বাংলা(কেষ্ট-রাই) মন্দির আর শ্যাম-রাই মন্দির দেখে নেওয়া যাবে। বিষ্ণুপুরের গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলি আরকিওলজিকল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সংরক্ষিত। ট্যুরিস্টদের থেকে মেনটেন্যান্স ফি হিসেবেই এই টাকাটা নেওয়া হয়। এই মন্দিরগুলো প্রত্যেকটিই এক একটা অসাধারণ শিল্পরীতির সাক্ষর বহন করে।
ভ্রমণ শুরু হল রাসমঞ্চ থেকে। রাসমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বীর হাম্ভীর (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ)।এটা ভারতের প্রাচীনতম পোড়ামাটির মন্দির। ইটের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা এই মঞ্চটি বর্তমানে একটি স্মৃতিসৌধ। শোনা যায় এই ভুলভুলাইয়ায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাস উৎসব পালন করা হত।
বিষ্ণুপুরের অন্যতম আকর্ষণ জোড়বাংলা(কেষ্ট-রাই) মন্দির আমাদের পরবর্তী গন্তব্য। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিং ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাসিকাল চালা শিল্পরীতি অনুযায়ী নির্মিত এই মন্দিরটি। এটি দেখলে মনে হবে দুটো কুঁড়েঘর একটা ছাদ আর দেওয়াল দিয়ে জোড়া। এর গাত্রে খোদিত টেরাকোটার কাজ অসাধারণ। তৎকালীন রাজাদের কীর্তি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত আছে এই টেরাকোটার কাজে ছবির মাধ্যমে।
টেরাকোটার কারুকাজ সমৃদ্ধ শ্যাম-রাই মন্দির ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মল্ল রাজা চৈতন্য সিং প্রতিষ্ঠা করেন। ডোম আকৃতির শিখর যুক্ত মন্দিরটির গায়ে পুরাণের কাহিনি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির দেওয়ালে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও গণেশাদি দেবতা, হাতি, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি পশুপাখি, নরনারী প্রভৃতি পোড়ামাটির মূর্তিদ্বারা সুন্দরভাবে অলংকৃত। শ্রী কৃষ্ণ এই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা।

এরপর আমরা গেলাম দুর্গের দিকে। পথে পড়ল গুমঘর। এটাই ছিল মল্ল রাজাদের আমলে কয়েদখানা। এরপর এল দুর্গের দরজা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম একটা ছোটো জলাধার। একে বলে মোর্চা হিল।এখানে দুর্গাপূজোয় কামান দাগা হত। আর একটু এগিয়ে দেখলাম পাথরের রথ। এটি ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরী। পরের গন্তব্য লালজি মন্দির আর রাধেশ্যাম মন্দির। রাজা বীরসিংহ কর্তৃক ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লালজি মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার চারচালা একচূড়া মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ৫৪ বর্গফুটের ভিত্তিবেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী মন্দিরটির পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তিনটি করে তোরণযুক্ত প্রবেশ পথ ও সংলগ্ন দালান আছে। চূড়ার নীচের খাড়া অংশের চারদিকে চারটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করে পঙ্খ আছে আর উপরের অংশে কার্নিসের প্রয়োগ, পীঢ়া দেউলদীর্ঘ আকৃতি এবং অলংকরণ মন্দিরটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।
শহরের জলাভাব মেটাতে মল্লরাজ বীরসিংহ বিষ্ণুপুরে অনেকগুলি দীঘি খনন করেন। লালবাঈ-এর গল্পকথা জড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত লালবাঁধকে ঘিরে। লালবাগ একটি স্মৃতি উদ্যান। কোনো এক মল্ল রাজা তাঁর মুসলমান স্ত্রী লালবাঈ-এর উদ্দ্যেশে এই উদ্দ্যানটি নির্মাণ করান। লালবাগ থেকে আমরা গেলাম দলমাদল কামান আর ছিন্নমস্তা মন্দির দেখতে। দলমাদল কামান এক ঐতিহাসিক সাক্ষী বহন করছে। কথিত আছে রাজা গোপাল সিংহ-এর আমলে গৃহদেবতা মদনমোহন স্বয়ং এই কামানের সাহায্যে বর্গী আক্রমণ রুখেছিলেন। ছিন্নমস্তা মন্দিরটি প্রায় একশ বছর পুরোনো। নিয়মিত এখানে পুজো হয় ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলে।
এবার ফেরার পালা। তার আগে অবশ্য ইতিহাস থেকে বাস্তবে ফিরে হোটেল মেঘমল্লারে পোস্তর বড়া দিয়ে জমিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।
~ বিষ্ণুপুরের তথ্য || বিষ্ণুপুরের আরো ছবি ~

অর্থনীতি ও প্রবন্ধন (ম্যানেজমেন্ট) বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ব্যাঙ্গালোরের আচারিয়া ও ক্রাইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা রিমি বর্তমানে দুর্গাপুরের ম্যানেজমেন্ট কলেজে আংশিক সময়ে পড়ান। বই পড়া, ছোটোখাটো লেখালেখি করা, গুছিয়ে সংসার করা ছাড়াও ঘুরে বেড়ানোর সখ।

|
![]()
ইচ্ছে হল
দেবশ্রী ভট্টাচার্য
"খুদ্ হি পেশ কর্ বুলন্দ ইতনি
কি খুদা খুদ্ বন্দে সে পুছে
বতা তেরা রজা কেয়া হ্যায়।।"
বরফের পাহাড় দেখব। এই ইচ্ছাতো মনের মধ্যে জমে উঠেছে কতদিনই। না দূর থেকে নয়, হাত দিয়ে ছুঁয়ে, ছুঁয়ে, অনুভবে। কত পাহাড়ইতো দেখলাম, গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়, রুক্ষ পাথুরে পাহাড়, দূর থেকে দেখা বরফের পাহাড়... আশ মেটে কই?
গ্যাংটকে পৌঁছে দেখলাম আমাদের হিসেবটা একেবারে নির্ভুল – কাটাও, ইয়ুমথাং, লাচুং কোথাও যেতে হবে না, ছাংগুতেই অনেক বরফ। কিন্তু তাতো হল, বরফে ঢাকা পথে যাওয়ার অনুমতি মিলবেতো, এবারে সেই চিন্তা শুরু হল।
এখানে পৌঁছানোর পর থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই সামনের এম জি মার্গে হাঁটতে বেরোলাম। আকাশে সাদা-কালো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এখানে বৃষ্টি মানে ছাংগুতে নিশ্চয় বরফ পড়ছে। মনে মনে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগলাম। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার সাব দরকারি কাগজপত্র নিয়ে পারমিটের ব্যবস্থা করতে গেছেন।
পরদিন সকালে বেরোনোর জন্য সবাই প্রায় তৈরি হয়েই গেছি, তখনই ফোন এল ছাংগু যাওয়ার পারমিট দেওয়া হচ্ছে না। অগত্যা গ্যাংটক সাইট সিয়িং। এদিন তবু ঘুরে বেরিয়ে কাটল। পরেরদিন আকাশের যা অবস্থা সারাদিন আমরা হোটেলের ঘরেই বন্দী থাকলাম। বিকেল বেলার দিকে মেঘগুলো আমাদের দুঃখী দুঃখী মুখ দেখে বোধহয় জানলার কাছে নেমে এসেছিল। খানিকক্ষণ মেঘের সঙ্গে খেলা করেই বেশ কাটল।
 তবে মনে হয় খুব মন দিয়ে কিছু চাইলে সেটা অবশ্যই পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে আকাশের ঝলমলে চেহারাটা দেখে সেই কথাটাই মনে হল। আমাদের মুখও আকাশের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফোন করে জানা গেল এদিনও পারমিট পাওয়া যাবেনা - মিলিটারি রাস্তা পরিস্কার করবে। আগামীকাল বেরোনো একেবারে পাক্কা। দুদিন যখন অপেক্ষা করতে পেরেইছি, তাহলে আর একদিনেই কীবা যায় আসে। আবহাওয়া পরিস্কার থাকায় সারাদিনটা আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েই দিব্যি কেটে গেল।
তবে মনে হয় খুব মন দিয়ে কিছু চাইলে সেটা অবশ্যই পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে আকাশের ঝলমলে চেহারাটা দেখে সেই কথাটাই মনে হল। আমাদের মুখও আকাশের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফোন করে জানা গেল এদিনও পারমিট পাওয়া যাবেনা - মিলিটারি রাস্তা পরিস্কার করবে। আগামীকাল বেরোনো একেবারে পাক্কা। দুদিন যখন অপেক্ষা করতে পেরেইছি, তাহলে আর একদিনেই কীবা যায় আসে। আবহাওয়া পরিস্কার থাকায় সারাদিনটা আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েই দিব্যি কেটে গেল।
পরদিন সকালবেলায় ঝলমলে রোদ্দুর মাখা পথে আমাদের গাড়ি পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল – মনে হল যেন অনন্ত প্রতীক্ষার শেষ হল। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফের দেখা মিলল। প্রথমে পাথরের খাঁজে খাঁজে সাদা চুনের ডেলার মত, কখনওবা পাহাড়ের গা দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঝুলছে পাহাড়ের গা বেয়েই। আরেকটু এগিয়ে দেখি যেদিকে দুচোখ যায় সবটাই সাদা – পাহাড়ের মাথা থেকে রাস্তা, পাহাড়ি ঘরগুলির ছাদ পর্যন্ত – যেন শ্বেত বসনা দেবী সরস্বতী বসে আছেন শ্বেত হংসের ওপরে।
ছাংগুতে পৌঁছে দেখি পুরো লেকটাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আশেপাশে ঘুরে বেরাচ্ছে চমরী গাইয়ের দল। মাত্র তিন-চার ঘন্টার মধ্যেই ৪,৫০০ ফুট উচ্চতা থেকে একেবারে ১০,৫০০ ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছি। আমার ছ'বছরের ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম ওর কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র খাইয়ে চাঙ্গা করে আবার রওনা দিলাম।
 এবার লক্ষ্য ভারত-চিন সীমান্তে নাথুলা আর ফেরার পথে বাবা মন্দির। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা পথ এগোতেই আর্মি পথ আটকালো - আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। সেখানেও আবার আর এক বিপত্তি – আমরা খেয়ালই করিনি যে সবারই বয়স অবিশ্বাস্যরকম ভুল লেখা ছিল। আর্মির জওয়ানটি একটুক্ষণ আমাদের সকলের দিকে বিস্ময়ে ভরা অবাক চোখে তাকিয়ে নেহাত বিরক্ত হয়েই বলল – ঠিক করকে লিখিয়ে। গাড়ির ড্রয়ার হাটকে একটা ভাঙ্গা পেন পাওয়া গেল, তাই দিয়েই কোনমতে কাজ চালানো হল। কিন্তু হায় এত করেও শেষ রক্ষা হল না। হঠাৎ গাড়ি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি শুধু আমাদের গাড়িই নয়, সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। সামনের রাস্তা বরফে-কাদায় মাখামাখি। চেষ্টা করেও গাড়ি আর এগোনো গেল না। অগত্যা নেমে পড়ে হাঁটার উদ্যোগ নিলাম। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে নাথুলা। এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে? রাস্তা বেশ পিছল তা হাঁটতে গিয়েই টের পেলাম। আরও ওপরে পৌঁছালে কীহবে কে জানে! তার ওপরে কয়েকটা গাড়ি ব্যাক গিয়ারে যখন ওঠার চেষ্টা করছে তখন আর হাঁটার জায়গাই থাকছে না। বিপদ বুঝে অ্যাডভেঞ্চারের আশা ত্যাগ করলাম।
এবার লক্ষ্য ভারত-চিন সীমান্তে নাথুলা আর ফেরার পথে বাবা মন্দির। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা পথ এগোতেই আর্মি পথ আটকালো - আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। সেখানেও আবার আর এক বিপত্তি – আমরা খেয়ালই করিনি যে সবারই বয়স অবিশ্বাস্যরকম ভুল লেখা ছিল। আর্মির জওয়ানটি একটুক্ষণ আমাদের সকলের দিকে বিস্ময়ে ভরা অবাক চোখে তাকিয়ে নেহাত বিরক্ত হয়েই বলল – ঠিক করকে লিখিয়ে। গাড়ির ড্রয়ার হাটকে একটা ভাঙ্গা পেন পাওয়া গেল, তাই দিয়েই কোনমতে কাজ চালানো হল। কিন্তু হায় এত করেও শেষ রক্ষা হল না। হঠাৎ গাড়ি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি শুধু আমাদের গাড়িই নয়, সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। সামনের রাস্তা বরফে-কাদায় মাখামাখি। চেষ্টা করেও গাড়ি আর এগোনো গেল না। অগত্যা নেমে পড়ে হাঁটার উদ্যোগ নিলাম। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে নাথুলা। এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে? রাস্তা বেশ পিছল তা হাঁটতে গিয়েই টের পেলাম। আরও ওপরে পৌঁছালে কীহবে কে জানে! তার ওপরে কয়েকটা গাড়ি ব্যাক গিয়ারে যখন ওঠার চেষ্টা করছে তখন আর হাঁটার জায়গাই থাকছে না। বিপদ বুঝে অ্যাডভেঞ্চারের আশা ত্যাগ করলাম।
ফেরার পথে পৌঁছালাম বাবা মন্দিরে। বাবা হরভজন সিং ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক জওয়ান। ১৯৬৫ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় কর্মরত অবস্থাতেই হিমবাহের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হরভজন সিংকে নিয়ে নির্জন এই পাহাড়ি অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে নানান উপকথার কাহিনি। এখানকার সেনা জওয়ানেরা বিশ্বাস করেন যে আজও তিনি তাঁদের পাহারা দেন, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ান। বাবা এখনও সরকারি বেতন আর ছুটি পান। বছরের কিছুটা সময় তাঁর ব্যবহৃত জামাকাপড় নিয়ে যাওয়া হয় পাঞ্জাবে তাঁর বাড়িতে, আবার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়ে আনা হয়।
এসব শুনতে শুনতে সত্যি যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মন্দিরে ঢুকে দেখি একপাশে সুন্দর করে একটা ক্যাম্পখাট পাতা, খাটের ওপরে বাবা হরভজন সিং-এর ইউনিফর্ম রাখা আছে। মাটিতে একপাশে রয়েছে পালিশ করা বুটজোড়া। প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। ফিরে এলাম ছাংগুতে।
এখানে এসে সবাই দারুণ খুশি। আমাদেরই মত নাথুলা দেখতে না পেয়ে ফিরে আসা পর্যটকে জায়গাটা ততক্ষণে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। এতদিনের অপেক্ষার পর হাতের কাছে অঢেল বরফ পেয়ে খানিকক্ষণ আমরা বড়রাও যেন আবার ছোট হয়ে গেলাম – বরফ ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা চলল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নীচে নামার রাস্তা ধরলাম।
ফিরে যেতে যেতে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল – ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই সমান সুন্দর। বরফের পাহাড় দেখে আজ সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু তাতে আমার এতদিনের অন্য সব দেখা, অন্য পাওয়া কোনটাই কমে যায়নি। যতদিন বেঁচে আছি দুচোখ ভরে তাঁর সব সৃষ্টি দেখতে চাই। যদি কোনদিন দেখা হয় সেই শিল্পীর সঙ্গে যেন বলতে পারি সেই অপূর্ব অনুভূতির কথা।
একটা ইচ্ছাপূরণের মনভরা আনন্দ যেন এই মুহূর্তে আরও বড় আর একটা ইচ্ছের জন্ম দিল।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দেবশ্রী ছোটবেলা থেকেই লিখতে ভালোবাসেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । কেদার ও গঙ্গোত্রী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রথম বই 'পাহাড়ের গান' প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের বইমেলায়।

|
||